চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ বাঙালি মুসলমানদের দু:সময়ের চাঞ্চল্যকর ইতিহাস
এম আর আখতার মুকুল
চিরস্থায়ী হিসেবে জমিদারির বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব করে ১৭৯৩ সালের ৬ই মার্চ লর্ড কর্ণওয়ালিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডনস্থ ডিরেক্টরদের কাছে লেখা চিঠিতে বললেন, “বেশ কিছু সংখ্যক নেটিভদের হাতে যে বিপুল পরিমাণে মূলধন রয়েছে, তা বিনিয়োগ করার আর কোনও পথ নেই। ….. তাই জমিদারির বন্দোবস্ত নিশ্চিত (চিরস্থায়ী) করা হলে শিগগির উল্লেখিত সঞ্চিত মূলধন জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ হবে।”
লর্ড কর্ণওয়ালিস –এর চিন্তাধারা ইংরেজদের দৃষ্টিকোন থেকে সময়োপযোগী ও সঠিক ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী, মুৎসুদ্দিগিরি, বেনিয়ানি এবং ব্যবসার মাধ্যমে কোলকাতার সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তা জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ হতে শুরু করল। এই নব্য ধনীরা দলে দলে নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিনত হলো।
লর্ড কর্নওয়ালিস এ সময় আর একটা অর্থসহ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন যে, প্রাচীন বনেদী জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে প্রাপ্য টাকা জমা দিতে অভ্যস্ত নয়। তাই সামান্যতম গাফিলতির দরুন এবং নতুন বন্দোবস্তের কড়া আইনের দরুন এসব জমিদারি একে একে নীলামে উঠতে লাগল। আর কোলকাতার নব্য ধনী মুৎসুদ্দি বেনিয়ানরা নীলাম থেকে এসব জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হলেন।
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার –এর (বেঙ্গল এম এস রেকর্ড চার ভলিউম, লন্ডন ১৮৯৪ : ১নং ভলিউম– ভূমিকা) বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৯৬–৯৮ সালের মধ্যে ৫৫ লাখ ২১ হাজার ২৫২ টাকার রাজস্বওয়ালা জমিদারি নীলামের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই টাকা মোট জমির প্রাপ্য খাজনার এক–পঞ্চমাংশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পরবর্তী ২২ বছরের মধ্যে বাংলার এক–তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পরিমান জমিদারি নীলামে বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়। অর্থাৎ বনেদী জমিদারদের হাত থেকে নব্য ধনীদের নিকট হস্তান্তর হয়।
উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, ১৮০০ সালের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালেই বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়িতেই বন্দি করা হয়। ১৭৯৫ সালের ২৭শে মার্চ গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল –এর নিকট দাখিলকৃত সিলেক্ট কমিটির এক রিপোর্ট বলা হয়, “বাংলাদেশের বাকি রাজস্বের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দু’জনের কাছে বাকি : বীরভুম ও রাজশাহীর জমিদার। সরকারি রাজস্ব থেকে নিজেদের ব্যভিচার ও বিলাসিতার জন্য প্রচুর অর্থ অপব্যয় করার দরুনই তাঁদের দেয় রাজস্ব তাঁরা দিতে পারেননি এবং তাদেরই বংশদের নির্দেশে জমিদারি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়।”
কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের এই নতুন গোত্রাস্তরিত জমিদার গোষ্ঠীর চরিত্র বনেদী জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁদের চাল–চলন, আচার–ব্যবহার এমনকি পোশাক–পরিচ্ছদ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ভিন্নতর। তাঁদের চাল–চলন, আচার–ব্যবহার এমনকি পোশাক–পরিচ্ছদ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল। নব্য জমিদাররা তাঁদের জমিদারিকে এক ধরনের ব্যবসা বলে মনে করতেন। তাই এরা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মধ্য স্বত্বভোগীদের বলগাহীন শোষণের লাইসেন্স প্রদান করল। এর ফলে গ্রাম বাংলায় নতুন শ্রেণী বিণ্যাসের সুচনা হলো।
লর্ড কর্ণওয়ালিসের আরও ধারনা ছিল যে, কোলকাতার ধনাঢ্য সুবর্ণ শ্রেণীর নব্য জমিদার হিসেবে গোত্রান্তর হলে এদের জীবনের নতুন প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি এবং এরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নতুন ধরণের বিলাসিতা এবং মামলা–মোকদ্দমায় ব্যয় করবে। কার্যক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর চিন্তা খুবই বাস্তবমুখী বলে প্রমানিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর এবং নব্য জমিদাররা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বিলাসিতা, যৌথ সম্পত্তির ভাট–বাটোয়ারা সংক্রান্ত মামলা–মোকদ্দমা এবং জমিদারিতে উদ্ধৃত প্রজাদের দমনে গুন্ডা ও লাঠিয়াল বাহিনী ভাড়া করা ইত্যাদি ব্যাপারে কত লাখ লাখ টাকা যে ব্যয় করেছে তার কোনও সঠিক হিসাব পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং নারী, মদ ও জুয়াখেলায় ব্যয়কৃত অর্থের পরিমানও কেউ বলতে পারে না।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় স্বল্প দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হলো জমির বর্গা প্রথা। এটাকে উত্তরবঙ্গ এলাকায় অধিয়ার প্রথা বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে এই প্রথা চালু হবার প্রাক্কালে বিত্তশালীরা বর্গাপ্রথার সুযোগে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে এক সঙ্গে বহু জমি কিনে মালিকানা লাভ করল। সে আমলে এ ধরনের জমির মালিকদের ‘লটদার’ বলা হতো। ‘লট’ হিসেবে জমি কিনত বলেই এদের লটদার নামকরণ হয়েছে। পরবর্তীকালে এরাই হচ্ছেন গ্রামবাংলার প্রতিক্রিয়াশীল ‘কুলাক’ (রাশিয়ায় জারের আমলে বিত্তশালী কৃষকদের কুলাক মলা বলা হতো) সম্প্রদায়। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ‘জোতদার শ্রেণী।’
এখানে লক্ষনীয় যে, ১৯৫৫ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও এই বর্গা প্রথা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে চালু রয়েছে। শুধু মাত্র ‘বর্গা প্রথা’ কে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে তেভাগা সংক্রান্ত কয়েকটি বিধি জারি করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পরবর্তী প্রায় পৌনে দু’শ বছর পর্যন্ত এই বর্গা প্রথায় চাষের জন্য বাংলার কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে। আলোচ্য সময় শুধুমাত্র জমির মালিকানার বদৌলতে জোতদাররা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকটা লাভ করত। অথচ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম থেকে শুরু করে কৃষি উপকরণ সবটাই ছিল অধিয়ার কৃষকদের দায়িত্ব। এর অন্যথা হলেই যথেচ্ছভাবে জমি থেকে বর্গাচাষিদের উচ্ছেদ করা হতো। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে জোতদার শ্রেণী গঠনের গোড়ার কথা।
বাঙালি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে দু:সময়
মুসলমান বিত্তশালীরা নিজেদের হাত থেকে ইংরেজদের কাছে শাসনভার চলে যাওয়ার ‘অভিমানে’ এবং একশ্রেণীর মোল্লা মৌলভীদের প্ররোচনায় শাসক গোষ্ঠীর প্রতি কিছুটা ‘অসহযোগীতা’ প্রদর্শনের জের হিসেবে সযত্নে নিজেদের দুরে সরিয়ে রাখায় হিন্দু বনিক, সরকারি কর্মচারী এবং বিত্তশালীরা জমির মধ্যস্বত্ব লাভের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে নতুন আর এক ধরনের ‘জমিদার শ্রেণী’ সৃষ্টির গোড়ার কথা।
এই জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এরই ফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই, যেসব বাঙালি হিন্দু বিত্তশালীরা ভারতের তৎকালিন কোলকাতা নগরীতে ইংরেজদের অনুকরণে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা করছিলেন, তাদের অনেকেই আবার জমির উপর প্রলুব্ধ হলেন এবং রাতারাতি জমিদার হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করলেন। এরই জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে দ্বারকানাথ ঠাকুর। ‘কার ঠাকুর কোম্পানি’ এবং রানীগঞ্জ কোলিয়ারীতে মুলধন বিনিয়োগ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবী ঠাকুরের পিতামত) একসময় বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত জমিদার পরিনত হলেন।
সে আমলের সার্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে প্রায় কয়েক দশক পর্যন্ত ‘অস্থিরতা আর আর অরাজকতা’র পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নয়া সহযোগী হিসেবে স্থানীয়ভাবে বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের মাঝ থেকে শহরভিত্তিক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, নানা ঘাত–প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে জমিদারি ও জোতদারি প্রথার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্নতাপ্রাপ্ত হলো। অবশ্য সমসাময়িক কালেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার এবং চাকরিজীবী প্রভৃতি পেশায় লিপ্ত (প্রায় সবাই হিন্দু) ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
(চলবে)
উৎসঃ কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি (পৃষ্ঠা ২৭–২৯)
এম আর আখতার মুকুল
এম. আর আখতার মুকুল (জন্ম: ৯ আগস্ট, ১৯৩০ - মৃত্যু: ২৬ জুন, ২০০৪)সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ‘চরমপত্র’-এর কথক। জন্ম ১৯২৯ সালের ৯ আগস্ট বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের অন্তর্গত চিংগাসপুর গ্রামে। পুরো নাম মুস্তাফা রওশন আখতার মুকুল। পিতা বিশিষ্ট সাহিত্যিক সা’দত আলি আখন্দ, মাতা রাবেয়া খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁকে একাধিকবার জেল খাটতে হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। জীবিকার জন্য তিনি বীমা কোম্পানি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন বিভাগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি সময় কেটেছে সাংবাদিকতার পেশায়। বিভিন্ন সময়ে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও পূর্বদেশ পত্রিকায় কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড প্রেস অফ পাকিস্তান (ইউপিআই)-এর ঢাকা ব্যুরো প্রধান ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গন পরিদর্শন শেষে তাঁর রচিত এবং স্বকণ্ঠে প্রচারিত ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমে তাঁকে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। ১৯৭২ সালে তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এ চাকরি হারিয়ে অনেক বছর তিনি লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন। এ সময় জীবিকার তাগিদে তাঁকে এমনকি পোশাক প্রস্ত্ততকারক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতে হয়েছে। ১৯৮৭ সালে দেশে ফিরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছুদিন কাজ করেছেন।পরে তিনি ঢাকায় সাগর পাবলিশার্স নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
এ সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর রচিত ৬০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পল্লী এক্সপ্রেস (অনুবাদ, ১৯৬০), রূপালী বাতাস (১৯৭২), রূপালী বাতাস সোনালী আকাশ (১৯৭৩), মুজিবের রক্তলাল (১৯৭৬), ভাসানী মুজিবের রাজনীতি (১৯৮৪), পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন (১৯৮৫), চল্লিশ থেকে একাত্তর (১৯৮৫), আমি বিজয় দেখেছি (১৯৮৫), বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন (১৯৮৬), লন্ডনে ছক্কু মিয়া (১৯৮৬), ওরা চারজন (১৯৮৬), কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি (১৯৮৭), বায়ান্নোর জবানবন্দী (১৯৮৭), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৯৮৭), লেছড়াগঞ্জের লড়াই (১৯৮৭), নকশালদের শেষ সূর্য (১৯৮৯), একাত্তরের বর্ণমালা (১৯৮৯), বিজয় ’৭১ (১৯৯০), আমিই খালেদ মোশাররফ (১৯৯০), মহাপুরুষ (১৯৯১), একুশের দলিল (১৯৯২), দুমুখী লড়াই: আমরাই বাঙালী (১৯৯২), আমাকে কথা বলতে দিন (১৯৯৩), বাংলা নাটকের গোড়ার কথা (১৯৯৪), কে ভারতের দালাল (১৯৯৫), খন্দকার থেকে খালেদা (১৯৯৬), একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা (১৯৯৭), বঙ্গবন্ধু (১৯৯৭), জিন্নাহ থেকে মুজিব (১৯৯৮) এবং ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা (১৯৯৯)। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ২০০৪ সালের ২৬ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। [বাংলা পিডিয়া]
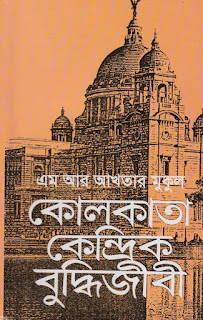
No comments:
Post a Comment